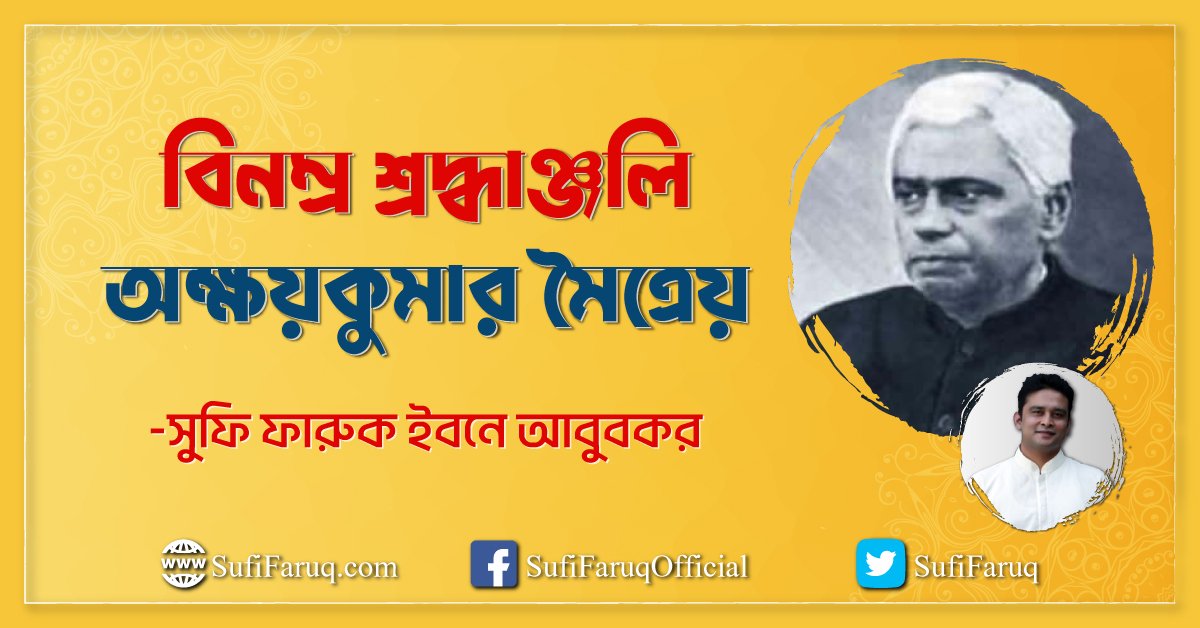বাংলা ইতিহাসচর্চার আধুনিক পথপ্রদর্শক, গবেষক–সমাজকর্মী ও আইনজীবী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আজও আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার নাম। দলিল–দস্তাবেজ, শিলালিপি, তাম্রশাসন—এ সবের নিখুঁত পাঠ ও বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি ইতিহাসকে কল্পকথা থেকে টেনে এনেছেন প্রমাণ–ভিত্তিক আলোচনার মঞ্চে। বাংলার অতীতের সঞ্চিত সত্য তিনি একাগ্র সাধনায় উদ্ধার করেছেন, স্থাপন করেছেন শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির দৃষ্টান্ত।

জন্ম, শিকড় ও শিক্ষাজীবন
অক্ষয়কুমারের জন্ম ১ মার্চ ১৮৬১, নওয়াপাড়া থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া গ্রামে—তখনকার নদিয়া জেলা; আজকের মানচিত্রে এটি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর অঞ্চলের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। জন্ম হয়েছিল মাতুলালয়ে (মায়ের মামার বাড়ি)। তাঁদের পূর্বপুরুষের শিকড় নওগাঁ জেলার গৌরনাই—বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। শৈশবে কুমারখালীর বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু কাঙাল হরিনাথ মজুমদার-এর কাছে তাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি। পরে রাজশাহীতে পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয়-র সংসর্গে বড় হয়ে ১৮৭৮-এ বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল (বর্তমান রাজশাহী কলেজিয়েট) থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৮০-এ রাজশাহী কলেজে এফ.এ., ১৮৮৩-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ., ১৮৮৫-এ রাজশাহী কলেজে বি.এল. পাস করে সেখানেই আইনচর্চা শুরু করেন।
চিন্তার ভিত: ইতিহাসের সত্য-অন্বেষণ
এফ.এ. শ্রেণিতে ম্যাকলে-র Clive and Hastings পড়ে যে “বিকৃত-ইতিহাস” তিনি শনাক্ত করেছিলেন, সেখান থেকেই তাঁর সংকল্প—বাংলার ইতিহাস বাংলারই ভাষায়, দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে লিখবেন। বহু বছর ধরে সাহিত্যিক উৎসের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে তিনি শিল্প-আইকনোগ্রাফি থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় ইতিহাস পর্যন্ত গভীর পাণ্ডিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন।
‘ঐতিহাসিক চিত্র’ ও এক ধারার সূচনা
১৮৯৯ সালে মৈত্রেয় সম্পাদিত ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ শিরোনামে বাংলা ভাষায় ইতিহাসভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধমালা/মনোগ্রাফ সিরিজ প্রকাশ শুরু হয়—যেখানে সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম, রানী ভবানী, সীতারাম, ফিরিঙ্গি বণিক প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব ও বহু স্থানের দলিলভিত্তিক আলোচনা ক্রমে পাঠকের মধ্যে ইতিহাস-অন্বেষার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। এটি বাংলা ভাষায় প্রত্নতত্ত্ব-অনুরাগ ও স্থানীয় ইতিহাসচর্চার এক যুগান্তকারী প্রবাহ তৈরি করে।
‘গৌড়লেখমালা’: শিলালিপি-তাম্রশাসনের ভাষান্তর
১৯১২ সালে প্রকাশিত ‘গৌড়লেখমালা’-তে তিনি পাল সম্রাটদের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনের মূল পাঠ ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন—বাংলা ভাষায় ইতিহাস-গবেষণার নতুন দ্বার খুলে যায় এখান থেকেই। আজও গবেষকেরা এই কাজকে মৌলিক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন।
বরেন্দ্র গবেষণা সোসাইটি ও জাদুঘর
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দিঘাপতিয়া রাজবংশের কুমার শরৎকুমার রায় ও শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ-এর সঙ্গে মৈত্রেয় মিলে প্রতিষ্ঠা করেন বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি (১৯১০) এবং একই বছরে রাজশাহী জাদুঘর (বর্তমান বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর)। সোসাইটির সভাপতি শরৎকুমার রায়, পরিচালক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সচিব রমাপ্রসাদ—মৈত্রেয় ছিলেন কার্যত দুই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ; ত্রিশ বছর ধরে তিনি অনুসন্ধানী সফরে অংশ নিয়ে বিপুল প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ করান।
পৌর নাগরিকতায় অবদান
রাজশাহী পৌরসভার কমিশনার থাকাকালে নগরের অবকাঠামো-সংস্কৃতি উন্নয়নে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। ডায়মন্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল-এ পৃষ্ঠপোষকতা, এমনকি রেশম-চাষ শেখাতে অবৈতনিক প্রশিক্ষক হিসেবে সময় দিতেন। সংস্কৃত নাট্যচর্চা ও চিত্রকলায়ও তিনি সক্রিয় ছিলেন; ছিলেন একজন ভালো ক্রিকেটারও।
‘ব্ল্যাক হোল অব ক্যালকাটা’—মিথের সমালোচনামূলক পুনর্বিচার
কলকাতার তথাকথিত ‘অন্ধকূপ হত্যা’-কাহিনি (Black Hole of Calcutta) নিয়ে ঔপনিবেশিক প্রচারণার অতিরঞ্জন ও অসঙ্গতি তিনি দলিল-প্রমাণে দেখিয়েছেন; বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী ১৯১৫/১৯১৬ সালে কলকাতার এক বিদ্বৎসভায় তিনি এই মিথ-নির্মাণের ইতিহাস-সমালোচনা উপস্থাপন করেন। (তারিখ ও আয়োজক সংস্থার উল্লেখে ভিন্নতা রয়েছে; কেউ এশিয়াটিক সোসাইটি, কেউ Calcutta Historical Society, এবং ২৪ মার্চ ১৯১৫/১৯১৬—দুই তারিখই আলোচিত।)
স্বীকৃতি ও সম্মান
জনসেবামূলক ও গবেষণা-কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ‘কায়সার-ই-হিন্দ’ স্বর্ণপদক (১৯১৫) এবং CIE—Companion of the Order of the Indian Empire উপাধি লাভ করেন।
সমকালীনদের মূল্যায়ন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চাকে “বাঙলা ইতিহাসে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন” বলেই অভিহিত করেছেন—অর্থাৎ দলিল-ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠতার যে ধারা তিনি আনলেন, সেটিই ইতিহাসকে মুক্তচিন্তার পরিসরে পৌঁছে দেয়। ইতিহাসবিদ আর.সি. মজুমদার তাঁর সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৮), মীর কাসিম (১৯০৬) ও গৌড়লেখমালা (১৯১২)-কে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসরচনার পথপ্রদর্শক কাজ হিসেবে অভিহিত করেন।
মানুষ অক্ষয়কুমার
আইনজীবী পেশায় সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত আবেগ ছিল ইতিহাস ও গবেষণা। একদিকে গ্রন্থাগার-দলিলের ধৈর্যশীল অন্বেষণ, অন্যদিকে মাঠে-ময়দানে প্রত্ন-উদ্ধার—দুই ধারাই তিনি সমান্তরালভাবে চালিয়েছেন। সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি ১৯৩০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—ফেলে যান এক বিরাট উত্তরাধিকার: সত্য-অন্বেষার ঐতিহ্য।
নির্বাচিত গ্রন্থাবলি (আংশিক)
- সমরসিংহ (১৮৮৩)
- সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৮)
- সীতারাম রায় (১৮৯৮)
- মীর কাসিম (১৯০৬)
- ঐতিহাসিক চিত্র (মনোগ্রাফ সিরিজ, সূচনা ১৮৯৯)
- গৌড়লেখমালা (১৯১২) — পাল সম্রাটদের শিলালিপি-তাম্রশাসনের বাংলা অনুবাদ-সহ সম্পাদনা।
- ফিরিঙ্গি বণিক (১৯২২)
- অজ্ঞেয়বাদ (১৯২৮)
কেন আজও প্রাসঙ্গিক
ঔপনিবেশিক পক্ষপাত-মুক্ত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চা, জাদুঘর-নির্মাণের পাবলিক হিস্ট্রি-বোধ, এবং আঞ্চলিক ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের মূলে সংযুক্ত করার প্রয়াস—এই তিন স্তম্ভে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আজও আমাদের দিশারি। তাঁর জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধা তাই কেবল স্মরণ নয়—সত্যের প্রতি অঙ্গীকার।