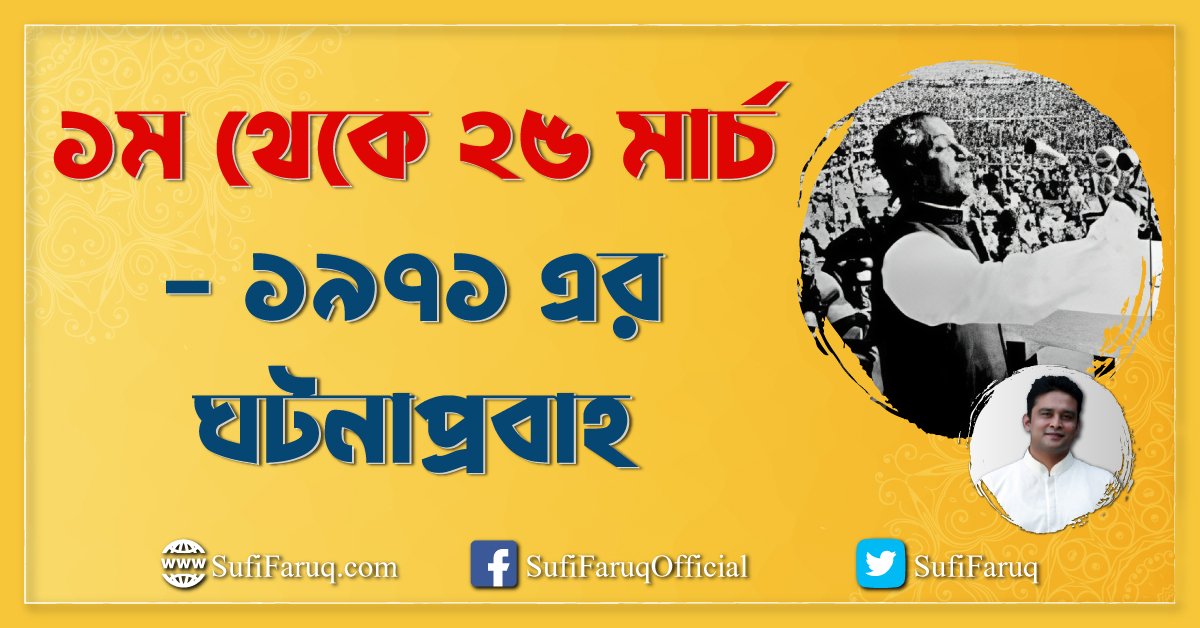১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অগ্নিগর্ভ সন্ধিক্ষণ। এই সময়টি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের নয়—এটি ছিল জনতার জাগরণ, আত্মদানের প্রস্তুতি, এবং স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা-উন্মুখ এক পর্ব। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিটি দিনের প্রেক্ষাপট, জনআন্দোলন, দমন-পীড়ন ও নেতৃত্বের পদক্ষেপ—যা স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি নির্ধারণ করে দেয়।
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এই সময়টিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা, জনতার জাগরণ, শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, এবং গণদাবির মুখে ইতিহাসের মোড় ঘোরানো একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। সেইসব ঘটনা না জানা থাকলে ’৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে।
আমি ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, মার্চ মাসের প্রতিটি দিন ছিল ঘটনাবহুল, প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ইতিহাসের নতুন বাঁক। এই প্রবন্ধে আমি ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ও নির্ধারক ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—যাতে করে পাঠকেরা সেই সময়ের স্পন্দনকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং নিজের মত গঠনের জন্য একটি প্রেক্ষাপট পান।
অগ্নিঝরা মার্চঃ বেদনার, সংগ্রামের, যুদ্ধের, স্বাধীনতার, মানবতার, স্বপ্নের আর বেঁচে থাকার মাস
স্বায়ত্তশাসনসহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির ছয়টি দাবি নিয়ে, ১৯৬৬ সালে, ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। এর অল্প সময়ের মধ্যেই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। চষে বেড়াতে শুরু করেন বাংলার মাঠ-প্রান্তর। এসময় ‘ছয় দফা: আমাদের বাঁচার দাবি’ শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে দেশজুড়ে বিলি করা হয়। তুমুল গণজোয়ার শুরু হয় ছয় দফার পক্ষে। তা দেখে ভয় সৃষ্টি হয় পাকিস্তানি জান্তাদের মনে।
ছয় দফা ঘোষণার পরের তিন মাসে দেশজুড়ে ৩২টি জনসভা করেন বঙ্গবন্ধু এবং প্রায় প্রতিবারই তাকে আটক করা হয়। অবশেষে বাঙালির জাগরণ দমানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদের জন্য জেলে ঢোকানো হয় জাতির স্বপ্নপুরুষ শেখ মুজিবকে। কিন্তু লাভ হয়নি। ছয় দফা ঘোষণা করে জাতীয় মুক্তির যে বীজমন্ত্র তিনি রোপণ করেছিলেন, তা ততদিনে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে গেছে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে।
এই ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে পুরো জাতি। যার প্রভাব পড়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। নৌকা প্রতীকের কাণ্ডারি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে ওঠেন অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা। কিন্তু পাকিস্তানি জান্তা ও নির্বাচনের পরাজিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা ষড়যন্ত্র করতে থাকে।
অনেক টালবাহার পর, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, স্বৈরাচার জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ দুপুরে, সেই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এরপরই ফুঁসে ওঠে আপামর বাঙালি। চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করার নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু।
মূলত, মার্চের প্রথম দুপুর থেকেই এই আন্দোলনের সূচনা। প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের অসহেযোগিতা করার নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু জান্তারা সেই আন্দোলনে গুলি চালিয়ে শতাধিক মানুষের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত করে তোলে। ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোর অবস্থানের নির্দেশনা দেন বাঙালির সর্বোচ্চ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।
২৫ মার্চ রাতে শুরু হয় গণহত্যা। ২৫ মার্চ এর আগে দিয়ে চলে গণহত্যার প্রস্ততি।
১ম থেকে ২৫ মার্চ – ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ
১–৬ মার্চ, ১৯৭১ : জাতীয় বিক্ষোভের সূত্রপাত এবং গণজাগরণের বিস্ফোরণ
১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংগঠিত রূপ নিতে শুরু করে। পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবার ছিলেন আরও বেশি সজাগ ও দূরদর্শী।
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট বিজয় বাতিল করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যেভাবে গণরায়ের অবমূল্যায়ন করেছিল, সেই অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আরও সতর্ক করে তোলে। জাতির সামনে তখন একটাই স্লোগান—
“জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু”
“বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর”
১ মার্চ: জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল, উত্তাল জনসাধারণ:
১ মার্চ, ১৯৭১—পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের ঘোষণা দেন।
এই ঘোষণা মুহূর্তেই দেশজুড়ে বিস্ফোরণ ঘটায় তীব্র বিক্ষোভের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ ও ৩ মার্চ সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেন।
২ মার্চ: বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা ওড়ে, শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন:
যদিও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতারাতি কারফিউ জারি করে, তবে ছাত্র, শ্রমিক, জনতা সে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেয়।
একাধিক স্থানে গুলি চালায় সেনাবাহিনী—শতাধিক নিহত, শত শত মানুষ আহত হয়।
এই দিনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত প্রথম পতাকা।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।
৩ মার্চ: জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ:
বঙ্গবন্ধু এই দিনটিকে “জাতীয় শোক দিবস” হিসেবে ঘোষণা করেন।
ঢাকায় পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পাঠ করা হয় “স্বাধীনতার ইশতেহার”।
এতে ঘোষিত হয়—
জাতীয় পতাকা
জাতীয় সংগীত
বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা
রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও কাঠামো
স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের নীতিগত রূপরেখা
৪ মার্চ: চট্টগ্রামে গণহত্যা, আন্দোলনে নতুন মাত্রা:
চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়।
“পিন্ডি না ঢাকা—ঢাকা, ঢাকা” স্লোগানে কাঁপতে থাকে শহর।
অস্ত্র সংগ্রহে নামে ছাত্র-যুব সমাজ, সর্বত্র গঠিত হতে থাকে সংগ্রাম কমিটি।
৫–৬ মার্চ: প্রশাসন অচল, বাঙালির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত:
দেশজুড়ে সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, আদালত, শিল্প-কারখানা বন্ধ থাকে।
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শহরের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত হয়।
রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র হতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় “ঢাকা বেতার কেন্দ্র” নামে এবং পিটিভি ঢাকা প্রচার করে “ঢাকা টেলিভিশন” নামে।
বেতার-টেলিভিশনে বাজতে থাকে দেশাত্মবোধক গান।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন,
“৭ মার্চ আমি জাতির সামনে চূড়ান্ত নির্দেশনা তুলে ধরবো।”
আন্দোলনের প্রকৃত রূপ: পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থার পতন:
এই কয়েকদিনেই পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি প্রশাসনের কর্তৃত্ব কার্যত ভেঙে পড়ে।
গণঅভ্যুত্থান ও অসহযোগ আন্দোলন এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে জনগণের কর্তৃত্বই পরিণত হয় বাস্তবতার নতুন রূপে।
৭ মার্চ ১৯৭১: চূড়ান্ত রণকৌশলের নির্দেশ দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিলেন বঙ্গবন্ধু
৭ মার্চ ১৯৭১—বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিনটি এক অবিস্মরণীয় টার্নিং পয়েন্ট। এদিন বিকেল ৩টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত রণকৌশলের দিকনির্দেশনা দেন।
সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢল নামে লাখো মানুষের। কয়েক বর্গমাইল এলাকা মানুষের উপস্থিতিতে উপচে পড়ে। চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে “তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ” স্লোগানে। উড়তে থাকে সবুজের মাঝে লাল সূর্যখচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত—প্রত্যেকে যেন প্রস্তুত স্বাধীনতার শপথে।
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মূল ঘোষণা:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন বলেন—
“আজ থেকে বাংলার সচিবালয়, কোর্ট-কাচারি, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সবকিছু অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। যতদিন না এ দেশের মুক্তি হচ্ছে, ততদিন কারও কাছে খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া যাবে না।”
তিনি নির্দেশ দেন—
প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের বেতন-ভাতা তুলতে পারে।
পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক টাকাও পাঠানো যাবে না।
রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, লঞ্চ, ট্রেন চালু থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়।
চাকরিজীবীরা ২৮ তারিখে অফিসে গিয়ে বেতন তুলবেন।
সবশেষে তিনি দেশের ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন—
“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”
অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:
এই ভাষণের পরপরই শুরু হয় দেশব্যাপী তীব্র অসহযোগ আন্দোলন। সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মচারী—সবাই এই নির্দেশনা অনুসরণ করে একযোগে পাকিস্তান সরকারকে অচল করে দেন।
বিশ্বজুড়ে এই ভাষণের প্রভাব ছিল অসাধারণ। এটি শুধু রাজনৈতিক ভাষণ নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য একটি রণকৌশলপত্র হয়ে ওঠে।
কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে বলেছেন “একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল”।
দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা এই ভাষণকে “স্বাধীনতার মূল দলিল” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব:
এই দিন ও ভাষণই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার পথে নিয়ে যায়। ৭ মার্চের ভাষণ আজ ইউনেসকো স্বীকৃত বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (Memory of the World)—যা ইতিহাসে বিরল সম্মান।
৮ মার্চ ১৯৭১: বঙ্গবন্ধুর ভাষণে স্বাধীনতার বার্তা ও ছাত্রসমাজের প্রতিরোধ পরিকল্পনা
১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল রাজনৈতিক অঙ্গনে ৮ মার্চ ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের দিন। এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া বক্তব্যে যেমন জাতির প্রতি দিকনির্দেশনা ছিল, তেমনি ছাত্রসমাজও গতি বাড়ায় তাদের আন্দোলনে। ফলে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট আরও দৃঢ় হতে থাকে।
এই দিন বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে প্রেস কনফারেন্সে মিলিত হন। সেখানে তিনি আগের দিন জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন—
“আমার দেওয়া সাত দফা দাবির মধ্যে যে কোনো একটিতেও আপস করা হবে না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলেও বাংলার মুক্তি মিলবেই।”
এই ঘোষণা জাতিকে আশ্বস্ত করে, তবে সরকারের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর আগেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, “৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।” পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এটিকে স্পষ্টতই একটি বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে। এমনকি ইসলামাবাদের সরকারি বেতার ও টেলিভিশনে ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়নি।
একইদিন ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারতসহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ঢাকায় তার বাসভবনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
এই সময়ে ছাত্রসমাজ ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল, সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা “বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো” স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে আসে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্ররা বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়। তাদের মুখে ছিল একটাই দাবি—বাংলাদেশের স্বাধীনতা।
ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন,
“বাংলাদেশ এখন কার্যত স্বাধীন। শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।”
ছাত্রদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদি আন্দোলন দমন করতে চায়, তবে ছাত্রসমাজ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তারা বঙ্গবন্ধুকে ৭ মার্চে দেওয়া শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানান।
সন্ধ্যায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা তার প্রতি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে জনগণের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান এবং পরদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।
৯ মার্চ, ১৯৭১ : স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে ছাত্রদের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও ভাসানীর হুঁশিয়ারি
৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের রেশ তখনও কাঁপিয়ে দিচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ। তাঁর দেওয়া অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশনা কী পরিমাণ কার্যকর হয়েছে—তার বাস্তব প্রমাণ মিলতে থাকে পরদিনের সংবাদপত্রেই।
অস্থানীয়দের ঢাকা ত্যাগ: জনমনের উত্তেজনা ও অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ:
৯ মার্চ, দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন—
👉 “অস্থানীয়দের ঢাকা ত্যাগের হিড়িক: এসব তবে কিসের আলামত?”
এই প্রতিবেদনে উঠে আসে, পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, পরিবারবর্গ ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।
জনগণের প্রতিরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের ভয়াল পরিণতির পূর্বাভাস হয়তো তাঁরা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।
ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক প্রস্তাব: স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়:
এই দিনেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সেখানে গৃহীত হয় দুটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব:
‘স্বাধীন বাংলাদেশ’ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বাংলাদেশে জাতীয় সরকার’ গঠনের আহ্বান।
তখনও “বাংলাদেশ” নামটি রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা হয়নি, কিন্তু ছাত্রসমাজের কল্পনায় স্বাধীন রাষ্ট্র ও সরকার তখনই রূপ পেতে শুরু করে।
এটি দেশের বহু জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রে বড় শিরোনামে প্রকাশ পায়, যা জাতির ভবিষ্যতের রূপরেখা অনেকটাই স্পষ্ট করে দেয়।
মওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারি: ১২ মার্চের আল্টিমেটাম:
এই দিনেই প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।
👉 তিনি ঘোষণা দেন:
“১২ মার্চের মধ্যে যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি ও শেখ মুজিব পুনরায় ১৯৫২ সালের মত একযোগে আন্দোলন করিব—প্রধানমন্ত্রী হইতে আমরা যাইবো না।”
এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, জাতীয় নেতৃত্ব তখন একই কণ্ঠে স্বাধীনতার আহ্বান জানাতে প্রস্তুত।
ভাসানীর এই বক্তব্য তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায় বড় শিরোনামে প্রকাশিত হয়।
🔍 সংক্ষেপে ৯ মার্চের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো:
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের নির্দেশনা আচরণে ও বাস্তবে প্রতিফলিত হতে শুরু করে
পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের ঢাকা ত্যাগে আতঙ্কের ইঙ্গিত
ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ‘স্বাধীন বাংলাদেশ’ ঘোষণার ঐতিহাসিক প্রস্তাব
বঙ্গবন্ধুকে ‘জাতীয় সরকার’ গঠনের জন্য ছাত্রদের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ
মওলানা ভাসানীর ১২ মার্চের আল্টিমেটাম ও সম্মিলিত আন্দোলনের ডাক
১০ মার্চ, ১৯৭১
“ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় ‘স্বাধীন বাংলাদেশ’ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন” শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। এ ছাড়া মওলানা ভাসানীর ভাষণ ও স্বাধীনতায় একাত্মতা প্রকাশের ব্যাপারে ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ দৈনিক সংবাদের শিরোনাম ছিল ‘মুজিবের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করিব : ভাসানী’। দৈনিক সংবাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘অশীতিপর বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল (মঙ্গলবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে অবিলম্বে বাংলার স্বাধীনতা প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। মওলানা বলেন, ‘১২ মার্চের মধ্যে যদি স্বাধীনতা দেওয়া না হয় তাহা হইলে আমি ও শেখ মুজিব পুনরায় ১৯৫২ সালের মত একযোগে আন্দোলন করিব, প্রধানমন্ত্রী হইতে আমরা যাইবো না।’
১১ মার্চ, ১৯৭১
বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর প্রশাসনিক কাজে যেন বাঙালিরা সহায়তা না করে। ৭ই মার্চের ভাষণে সেটা বলেছিলেন তিনি। তাঁর কথা কার্যকর হয় মাত্র পাঁচ দিনের মাথায়। ১৯৭১ সালের ১১ মার্চ সরকারি ও আধা সরকারি প্রায় সব কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। আদালত থেকে শুরু করে অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তাই স্বাধীনতার ডাককে সমর্থন করে কর্মস্থল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বের হয়ে আসেন।এমনকি সিনেমা শুরুর আগে, সিনেমা হলেও পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানটি বাজানো শুরু হয়। এটি ছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের প্রথম বর্ষণ মাত্র।
তবে কূট-কৌশলী ভুট্টো এক তারবার্তায় বঙ্গবন্ধুকে জানান, তিনি ঢাকায় এসে কথাবার্তা বলতে রাজি। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান মারাত্মকভাবে অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে যাচ্ছিল। ১১ মার্চ থেকে দেখা যায় পাকিস্তানের বড় পত্রিকাগুলো কাগজের সংকটে পড়েছে। সংকট এত তীব্র ছিল যে ডনের মতো বড় পত্রিকাও ১৪ পৃষ্ঠা থেকে ১০ পৃষ্ঠা ছেঁটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ তাদের নিউজপ্রিন্টের কাগজ যেত খুলনা নিউজপ্রিন্ট থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে কাগজের চালান বন্ধ করে দেয় খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল। এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে জানিয়ে সেদিনই ইয়াহিয়া খান ব্যবসায়ীদের একটি বার্তা দেন।
১২ মার্চ, ১৯৭১
লাহোরে সেদিন একটি সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে এয়ার মার্শাল আজগর আলি খান বলেন, লাহোরের জন্যই ঢাকার এই অবস্থা। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে অবস্থা আরো অবনতির দিকে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। অন্যদিকে ধীরে ধীরে পাকিস্তানের প্রতি ক্ষোভ ফুঁসে উঠছিল। পাকিস্তান সরকার থেকে পাওয়া পদবি ফিরিয়ে দেন জাতীয় পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ জহির উদ্দীন। ১৫ সদস্যের একটি দল বগুড়ার জেল থেকে পালিয়ে বের হয়। লন্ডনের ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-এ ছাপা হয়, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের শক্তি প্রয়োগ করা হবে ভুল সিদ্ধান্ত ও অকার্যকর।
এদিকে জাতীয় পরিষদ বেশ পাকাপোক্ত হয়ে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। সুফিয়া কামালকে সভাপতি মেনে সারা আলীর তোপখানা রোডের বাসায় মহিলা পরিষদের একটি সভা হয়। পাড়ায় পাড়ায় মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান জানানো হয়।
১৩ মার্চ, ১৯৭১
ইত্তেফাকে প্রাধান্য পায় মহিলা পরিষদের খবর। সংবাদের শিরোনাম ছিল, ‘পাড়ায় পাড়ায় মহিলা সংসদ গঠনের আহ্বান’। অন্যদিকে প্রশাসন প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ সব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বলা হয়, ১৫ তারিখের মধ্যে যোগ না দিলে বেতন বাতিল ও বহিষ্কার করা হবে। মার্শাল ল ও ১১৫ ধারা জারি হয়। এ ঘটনাকে বঙ্গবন্ধু এক ধরনের উসকানি বলেও মন্তব্য করেন। সেদিন শিল্পী জয়নুল আবেদিন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাওয়া পদবি ও বিশেষ পুরস্কার ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে পাকিস্তানিরা বড় হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি নিচ্ছিল চুপিসারে।
তারই ধারাবাহিকতায় বিদেশি কূটনীতিকদের অপসারণ করা হচ্ছিল ধীরে-সুস্থে। মার্চের ১৩ তারিখেই অপসারণ করা হয় পশ্চিম জার্মানির ৬০ জন, জাতিসংঘের ৪৫ জন, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্সের ৪০ জনসহ মোট ২৬৫ জন বিদেশিকে।
১৪ মার্চ, ১৯৭১
রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। সংগ্রাম দানা বাঁধতে শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গায়। বঙ্গবন্ধু এই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো আবারও অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সবাইকে আহ্বান করেন। তিনি সেদিন বঙ্গবন্ধু তার বিবৃতিতে বলেন, ‘… আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারে, সেজন্য আমরা মরতেও প্রস্তুত।… মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।… বাংলাদেশের মুক্তির উদ্দীপনা নিভিয়ে দেওয়া যাবে না।’
পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক নতুন ফর্মুলার কথা বলেন। সেখানে তিনি জানান পাকিস্তানের দুই বড় দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখাও করতে চান। দিন দিন লাহোরের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তান যেমন কাগজ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো চালানই গ্রহণ করা হচ্ছিল না। ১৪ তারিখ হঠাৎ খবর আসে ঢাকায় পাঠাতে না পারায় লাহোরে মণের পর মণ ফল নষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা থেকে পানের চালান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় করাচিতে পানের দাম বেড়ে দেড় শ রুপি হয়ে যায়।
১৫ মার্চ, ১৯৭১
পাকিস্তানি স্বৈরাচার জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় আসে ১৫ মার্চ। কালো পতাকা দেখানো হয় তাকে। কোথাও কোথাও স্বাধীন বাংলার পতাকাও ওড়ানো হয়।
‘বাঁচাও! বাঁচাও! বাংলার অসহযোগে পশ্চিমা শিল্পপতিদের নাভিশ্বাস’। ১৫ মার্চের দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম। এই সংবাদে করাচি, লাহোরসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাবসায়িক ভঙ্গুর অবস্থার কথা বলা হয়। লেখা হয়, ‘করাচীতে বর্তমান প্রতি সের পান ১৫০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ঢাকা হইতে পান না যাইতে পারায় করাচীতে পান বিরল হইয়ে পড়িয়াছে।’ সেদিন গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা ঘটে। একটি হলো করাচিতে ভুট্টো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শেখ মুজিবকে নিয়ে সরকার গঠন করা উচিত। আর দ্বিতীয় হলো প্রায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢাকায় আসেন ইয়াহিয়া খান। বিমানবন্দরে সাংবাদিক ছিল নিষিদ্ধ।
মূলত দুটি ব্যাপারই ছিল এক প্রকার ফাঁদ। কিন্তু এই ফাঁদের যোগ্য জবাব দেন শেখ মুজিব সেদিনই। তিনি বলেন, ‘কে আসল বা কে কী বলল, তা নিয়ে আমরা ভাবছি না। অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেই যাব।’ তিনি সেদিন আরো বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেন। যেগুলো পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক কৌশলকে আরো দুর্বল করে দিয়েছিল। এ দিন বেতারের সব কর্মকাণ্ড বাংলায় প্রচলন করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
১৬ মার্চ, ১৯৭১
১৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে আটটি পয়েন্টে আগের দিন (১৫ মার্চ ১৯৭১) দেওয়া দিকনির্দেশনা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়া হয়—‘সর্বসাধারণের প্রতি আমার নির্দেশ’। এ ছাড়া সেই প্রতিবেদনের নিচেই আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় এই শিরোনামে—‘চট্টগ্রামে বেতার কেন্দ্রে সকল কাজে বাংলা প্রচলনের সিদ্ধান্ত’।১৬ মার্চ থেকে শুরু হয় আলোচনা। মূলত আলোচনার নামে পাকিস্তানিরা সময়ক্ষেপণ করছিল এবং তাদের সেনাবাহিনী ও অস্ত্র আনছিল। সেদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আসেন দেখা করতে। রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।
১৭ মার্চ, ১৯৭১
দেশের সংকটময় অবস্থায়ও শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে বিভিন্ন সংস্থা ও শিল্পীরা শুভেচ্ছা জানাতে আসে। এর মাঝেই ইয়াহিয়া খান বৈঠকে বসতে চান। বঙ্গবন্ধু নিজের জন্মদিনে দ্বিতীয় বৈঠকে বসেন। সেদিনও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে আলোচনা চলছিল বেশ। সেদিন নিউজউইকের একটি নিজস্ব পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। সেখানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্তমান সিদ্ধান্ত যে অকার্যকর ও ভুল, সেটি উল্লেখ করা হয়।
সেখানে আন্তর্জাতিক বিখ্যাত কূটনীতিকদের বিভিন্ন মতামত সামনে রেখে প্রতিবেদক লোরেন জেনকিনসন লেখেন ‘পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হবে এটা কোনো প্রশ্ন নয়। বরং পরিস্থিতি হঠাৎ এতদূর গড়িয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল কি পরবর্তী সপ্তাহে কিংবা আগামী মাসে অথবা দুই বছর পর বিচ্ছিন্ন হবে এটাই প্রশ্ন।’ সেদিন ভারত প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের আকাশসীমায় বাংলাদেশগামী উড়োজাহাজ নিষিদ্ধ করে দেশটি।
১৮ মার্চ, ১৯৭১
‘ভারতের উপর দিয়া বাংলাদেশগামী সকল বিদেশী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ’। এটি ছিল ১৮ মার্চ ১৯৭১ সালের দৈনিক সংবাদের একটি প্রতিবেদন। সেখানে লেখা হয়, ‘ধারণা করা হইতেছে যে, বিদেশি বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে গোলযোগপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য বহন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।’
১৯ মার্চ, ১৯৭১
এই দিন ইত্তেফাকের খবর—‘আমি শেখ মুজিব বলছি : এ তদন্ত কমিশন চাহি নাই’। তার পরও সেদিন তৃতীয় দফায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। সেদিন প্রথমবারের মতো সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ জনগণের একটি সংঘর্ষ হয় ঢাকার বাইরে জয়দেবপুরে। মূলত সামরিক বাহিনীর অতর্কিত হামলার কারণেই সংঘর্ষের সৃষ্টি। এলাকায় জারি হয় কারফিউ।
২০ মার্চ, ১৯৭১
চতুর্থবারের মতো বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। ৯০ মিনিটের সেই বৈঠকে শুধুই সময় নষ্ট করেন ইয়াহিয়া। সেদিনের ইত্তেফাকে ছাপা হয়, ভারতের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড ও তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।
২১ মার্চ, ১৯৭১
ভোর ৬টা। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ প্রথম পতাকা উত্তোলন করে। সকাল ৯টায় তারা পল্টনে জয়বাংলা কুচকাওয়াজ করে। দুপুর ১টায় বায়তুল মোকাররমে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেদিন ভুট্টো গোপনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। তবে ঢাকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। প্রত্যেক বাসার ছাদে উড়ছিল বিভিন্ন আকৃতির পতাকা। যার মধ্যে ফুটে আছে বাংলাদেশের মানচিত্র। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফের বৈঠক করেন ইয়াহিয়া।
২২ মার্চ, ১৯৭১
বঙ্গবন্ধু তাঁর দাবিতে অনড়। ভুট্টোর উপস্থিতিতে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক চলে। মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মায় এবার হয়তো এসব শেষ হতে চলেছে। হয়তো নাটকীয় সিদ্ধান্ত আসবে। নয়তো সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে। পরের দিনের পত্রিকাগুলোতেও এর ছাপ লক্ষ করা যায়। সেদিন ছাত্রসংগ্রাম সংসদ একটি যুগোপযোগী কাজ করে। তারা একটি পরিকল্পিত পতাকার মাপ ও বিবরণ প্রকাশ করে, যা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে পাকিস্তানি কৌশলের কফিনে শেষ পেরেক ছিল।
২৩ মার্চ, ১৯৭১
২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে পালনের নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি ধানমন্ডির নিজ বাড়িতেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন এদিন। দেশজুড়ে শুরু হয় পাকিস্তানি পণ্য বর্জন।সব বড় অফিস বন্ধ। ২৩ তারিখ পাকিস্তান দিবস থাকলেও শুধু প্রেসিডেন্টের বাসভবনে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত ছিল। আর কোথাও দেখা যায়নি। পাকিস্তান দিবসে বরং উড়ছিল বাংলাদেশের নতুন পতাকা।
২৪ মার্চ, ১৯৭১
ছোট ছোট পাকিস্তানি দল ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করে। ইয়াহিয়া-মুজিবের দফায় দফায় বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত না এলেও ‘কোনো প্রকার নতি স্বীকার করা হবে না’ বলে সাফ জানিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ‘আওয়ামী লীগের বক্তব্য শেষ। আর অপেক্ষা নয়। দিনের পর দিন অপেক্ষা চলে না।’ সেদিন ঢাকার মিরপুরে একটি বাড়ি থেকে বাংলাদেশি পতাকা নামাতে বাধ্য করা হয়। আরেক জায়গায় একজন শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করা হয়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করলেও পাকিস্তান আর্মি তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেয়।
২৫ মার্চ, ১৯৭১
২৫ মার্চ এর ঘটনাপ্রবাহ : ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান সাদা পোশাকে গোপনে ঢাকা ছেড়ে চলে যান। ২৫ মার্চ এই খবর পাওয়া মাত্র, দলীয় নেতাকর্মীদের মাধ্যমে, দেশের সব প্রান্তে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বার্তা পাঠাতে শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনারা। ২৫ মার্চ সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি বলেন, ‘…এটাই সম্ভবত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।… পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন….।’ (অনূদিত)। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর তথা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর নিজের কণ্ঠের এই ঘোষণা বিশেষ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সম্প্রচারিত করা হয়। ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের নোঙর করা এক বিদেশি জাহাজও এই বার্তা গ্রহণ করে। ২৫ মার্চ রাতেই চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এই বার্তা কপি করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন।
২৭ মার্চ, ১৯৭১
আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান পত্রিকগুলোতে এই স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ফলাও করে প্রচার করে। ব্রিটেনের ‘দ্য টাইমস’ পত্রিকার শিরোনামে বলা হয় ‘…শেখ মুজিব ডিক্লেয়ার্স ইস্ট-পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট’। দ্য গার্ডিয়ানের সংভাদে বলা হয়, ‘একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে’। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ও দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকাতেও শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।
ব্যাস, শুরু হয়ে যায় যায় মুক্তিযুদ্ধ। সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশ পাওয়ার পর দলে দলে যুদ্ধে যোগ দেন কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-জনতা সবাই। বঙ্গবন্ধুর নামে পরিচালিত হতে থাকে এই যুদ্ধ। অবশেষে ত্রিশ লাখ মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা।
বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ, যাকে কেন্দ্র করে দুহাজার বছরের লালিত স্বপ্ন পূরণ করেছি আমরা। শোষিত মানুষের জন্য সংগ্রামী চেতনার কারণে স্বাধীনতার পর বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে বিশেষ মর্যাদা পান তিনি। বাঙালির মুক্তিদাতা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর, একজন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বনেতা।